বন্ধু চল্
#friends
#pennstate
#funnypeople
আমার আমেরিকায় ছাত্রাবস্থা ১৯৮৭ থেকে ১৯৯২ (অয়নের ১৯৮৬ – ১৯৯১)। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে। আমাদের বয়স যে শুধু অনেক কম ছিল তা নয়, আমাদের দেশটাও মুক্ত অর্থনীতির দেশ ছিল না। কোকা কোলা পাওয়া যেত না, টেলিভিশনে কেবলমাত্র দূরদর্শন, সকাল সাড়ে সাতটার খবর আর পৌনে আটটার রবীন্দ্রসঙ্গীত সব বাড়ির রেডিও থেকে বাজতে থাকত। আমেরিকায় পড়তে যাওয়া আজকের মত জলভাত ছিল না, আমেরিকার life style সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান থাকত সীমিত। আজকাল কি হয় জানি না, কিন্তু তখন বাংলাভাষীরা একজোট হয়ে থাকত। এমন নয় যে আমাদের বিদেশী বন্ধু ছিল না – অবশ্যই ছিল, অনেকে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠও ছিল। তবুও শুক্রবার রাতের আড্ডার আসর বাগীশা-পিকলুর বাড়িতেই বসত। Trivial Pursuit বলে একটা খেলার নেশা ধরে গেছিল। অভিজিৎ, পিকলু আর বাগীশার ব্রিজ খেলার সূচনাও এই সময়েই। এখন তো তারা রীতিমত Bridge Competition-এ খেলে।
Penn State-এ সেই সময়ে হয়ত জনা বারো-পনেরো বাঙালী ছাত্র ছিল, প্রায় সবাই PhD করছে। দু-একজন একটু সিনিয়র, দেশে কয়েক বছর চাকরি করে আবার পড়াশোনা শুরু করেছেন। কিন্তু বেশির ভাগই আমার মত, সদ্য MSc বা BTech করে চলে এসেছে। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ছিল অভিজিৎ দত্ত আর জয়ন্ত পান্ডা, একটা অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের একতলায় থাকতাম অয়ন আর আমি, দোতলায় অভিজিৎ আর জয়ন্ত। অভিজিৎ Chemical Engineering-এর ছাত্র, আর জয়ন্ত Aerospace Engineering-এর। ওদের বাড়িতে একটা তাজমহলের ছবি ছিল, সাদা তাজ, সামনের জল, যেখানে তাজের ছায়া পড়েছে, পেছনে যমুনা দেখা যাচ্ছে। পুরোটা সেলোফান কাগজে মোড়া। ছবিটা সম্ভবত ওরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল। ভারতীয় ছাত্ররা অনেকেই চলে যাবার সময় বন্ধুদের sublet করে দিত। মানে Realtor-এর খাতায় যাদের নাম রয়েছে, হয়ত তাদের মধ্যে একজন থাকছে, দ্বিতীয় জনের বদলে তৃতীয় আর একজন এল, কিন্তু Realtor-এর খাতায় তার নাম উঠল অনেক পরে। আমরাও সেই ভাবেই ঢুকেছিলাম, নয়ত ভালো অ্যাপার্টমেন্টের জন্য অনেক লাইন থাকে। উত্তরাধিকার সূত্রে অভিজিৎ-জয়ন্ত অনেক ছাতা গজানো মশলাপাতিও পেয়েছিল। আমার ধারণা সেগুলো ওরাও ওদের উত্তরসূরীদের জন্য রেখে গিয়েছিল।
একদিন অভিজিৎ-জয়ন্তর বাড়ি গিয়ে দেখি তাজমহলের সামনের সেলোফেনটা এক টানে ছেঁড়া।
- এ কি! কি হল?
- কালকে মামু অনেক মাল খেয়েছিল। তারপর মামুর মনে হল যমুনায় জল তুলতে যাবে। সেলোফেনটা থাকায় জল তুলতে পারছিল না, তাই ওটাকে ছিঁড়তে হল।
- আর তুমি কি করছিলে? আটকাতে পারলে না?
- আমাকেও তো সঙ্গে যেতে হল। এতো মাল খেয়েছে, যদি যমুনায় ডুবে যেত?
অভিজিতের নিক নেম ছিল মামু। জয়ন্তরই দেওয়া, তবে আমরা সবাই ব্যবহার করতাম।
জয়ন্ত আর অভিজিতের কাজ করার সময়ের ঠিক-ঠিকানা ছিল না। অনেক দিন হয়ত রাতে ডিপার্টমেন্টেই কাটিয়ে দিত। বিশেষ করে জয়ন্ত। Aerodynamics-এর মডেল তৈরী করা, তার বিভিন্ন experiment করা, ইত্যাদিতে অনেক সময় লাগত। জয়ন্ত যখন ফিরত, অভিজিৎ যেত কাজে। কথায় বলে না, চোরে কামারে মুখ দেখাদেখি হয় না – জয়ন্ত-অভিজিতেরও সপ্তাহের মধ্যে প্রায় সেই অবস্থা। ভোর রাত্তিরে বাড়ি ফিরে খানিকটা দুধ-কর্নফ্লেক্স খেয়ে জয়ন্ত যখন ঘুমতে গেল, অভিজিৎ ঘুম থেকে উঠল তার দু ঘন্টা পরে। দেখল ফ্রিজে আর দুধ নেই। কোঈ বাত নেহি – অভিজিৎ অরেঞ্জ জুস দিয়ে কর্নফ্লেক্স খেয়ে ডিপার্টমেন্টে চলে গেল। রান্নাবান্নাও যে যখন সময় পেত করে নিত, কিংবা বাগীশার বাড়ি তো আছেই। কখনো বা জয়ন্ত হয়ত ফোন করে ডাকত,
- আজ মামু চিকেনটা যা বানিয়েছে না, তোরা চলে আয়!
তবে এর উল্টোটাও হত। একবার অভিজিৎ কোনো একটা কনফারেন্স থেকে শুক্রবার বিকেলে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফিরে দেখে জয়ন্ত সোফায় শুয়ে আরাম করছে। বাড়িতে খাদ্যবস্তু কিছু আছে কি না জানতে চাইলে জয়ন্ত নাকি পা নাচাতে নাচাতে বলেছিল, “কাল রাতে শ্রবসী খেতে বলেছে”।
আমার নানা রকম রান্নাবান্নার ওরা ছিল গিনিপিগ।
জয়ন্তর মা হঠাৎ চলে গেলেন। জয়ন্ত দেশে এল। শীতকাল, জানুয়ারি মাস, State College-এর আবহাওয়া খুব খারাপ। পুরো Northeast-এই বরফ পড়ছে। জয়ন্তর ফেরার কথা, কিন্তু কোনো খবরাখবর পাওয়া যাচ্ছে না। অভিজিৎ এয়ারলাইন্সের অফিসে ফোন করল,
- Jayant Panda is supposed to be returning in this flight. Can you please give me some update?
সত্যি মিথ্যে জানি না, অভিজিৎকে এয়ারলাইন্সের মহিলা নাকি বলেছিলেন
- Are you kidding me? No Giant Panda can fly.
আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে জয়ন্ত প্রথম গাড়ি কিনল। মেরুন Subaru Station Wagon। আমি বেজায় খুশি, শনি-রবিবার চাইলেই Nittany Mall যাওয়া যাবে। Nittany Mall-ই তখন আমাদের কাছে একমাত্র বেড়াতে যাবার জায়গা, হয়ত পাঁচ-ছয় মাইল হবে, দশ কিলোমিটার। বাসে যাওয়া যায়, কিন্তু অনেক কেনাকাটি করে বাড়ি নিয়ে আসা সমস্যা। বাস স্টপ থেকে আমাদের বাড়ি অন্তত এক মাইল। অতএব বন্ধুবান্ধবের গাড়িই ভরসা। অকারণ পুলকে বাড়ির কাছের Weis Market ছেড়ে দূরের বড় Weis Market-এ যাওয়া হল একদিন। Weis Market ছিল আমাদের grocery store। এ ও একটা নতুন ব্যাপার। বিদেশে যাওয়ার আগে জানতাম grocery store মানে হল মুদীর দোকান। Greengrocer বলে একটা কথা দু-একবার কানে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, যেখানে আলু, পেঁয়াজ, কলা থেকে শুরু করে ওষুধ অবধি পাওয়া যায়, তাকে grocery store বলে, এটা জানতাম না। Pennsylvania-তে না হলেও Texas সহ অন্য অনেক জায়গাতে grocery store-এ বিয়ারও পাওয়া যেত।
একদিন রাত দশটায় হঠাৎ জয়ন্ত আমাদের বাড়ি এসে বলল, “চল, আমরা এখন ড্রাইভে যাই”। আমরা একবাক্যে রাজি, এক পায়ে খাড়া। একটা বড় কোট গায়ে চাপিয়ে পার্কিং লটে গিয়ে দেখি গাড়ি নেই।
- জয়ন্ত, গাড়ি কোথায় তোমার?
- সে কি রে! গাড়ি তো এখানেই ছিল।
- দ্যাখো, দ্যাখো, ভুলে অন্য কোথাও পার্ক করেছ না কি”?
পুরো পার্কিং লটটা একবার চক্কর দেওয়া হল। গাড়ি নেই। কয়েকটা ছোট ছোট গাছ ছিল লটের ধারে। জয়ন্ত সেগুলোর ডালপালা সরিয়ে গাড়ি খোঁজার চেষ্টায় ছিল। বললাম, “তোমার গাড়ি তো খেলনা নয় যে ওই গাছের পেছনে কেউ লুকিয়ে রাখতে পারে। বরং পুলিশে খবর দেবে কি না ভাবো”। যদিও গরীব graduate student-দের second hand Subaru গাড়ি চুরি হয়েছে শুনলে পুলিশও হেসে ফেলবে হয়ত। জয়ন্ত বলল, “আচ্ছা, দাঁড়া, একবার ডিপার্টমেন্টে দেখে আসি”।
পনেরো মিনিট পরে উত্তেজিত ফোন, “পেয়েছি, পেয়েছি, গাড়ি ডিপার্টমেন্টের পার্কিং-এ”।
তখন বোঝা গেল জয়ন্ত রবিবার গাড়ি চালিয়ে ডিপার্টমেন্টে গেছিল। Graduate student-দের সপ্তাহের মধ্যে ক্যাম্পাসে গাড়ি নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। খুব সিনিয়র ফ্যাকাল্টি ছাড়া কেউ অফিসের পাশে পার্কিং পেতেন না। এমনকি জুনিয়ার ফ্যাকাল্টিরাও পার্ক করতেন ক্যাম্পাসের বাইরের দিকে। সেখান থেকে ক্যাম্পাস লুপ, অর্থাৎ Penn State-এর নিজস্ব বাস ধরে সবাইকে অফিসে যেতে হত। যারা দূর থেকে আসতেন, তাঁরা তাই করতেন। আমরা যে দূরত্বে থাকতাম, তাতে হেঁটে যেতে কোনো অসুবিধে ছিল না। বরং সেটাতেই আমরা অভ্যস্ত ছিলাম। একমাত্র শনিবার আর রবিবার পার্কিং-এর কড়াকড়ি ছিল না। জয়ন্ত শখ করে গাড়ি নিয়ে গেছিল, এবং বেমালুম ভুলে গিয়ে রাতে হেঁটে বাড়ি ফিরেছে। সোমবার হেঁটে গেছে, হেঁটে এসেছে, মঙ্গলবারও তাই। নেহাৎ রাতে ড্রাইভে যাবার শখ হয়েছিল তাই, না হলে আরো কয়েকদিন হয়ত গাড়ি ক্যাম্পাসেই পড়ে থাকত। এবং আরো পার্কিং টিকিট জমা হতে থাকত।
জয়ন্ত আর অভিজিৎ দুজনে ভিন্ন প্রকৃতির বলেই বোধহয় বেশ অনেকগুলো বছর কোনোরকম অবনিবনা না হয়ে রুমমেট থাকতে পেরেছিল। Penn State-এ থাকার পুরো সময়টা অভিজিৎ গাড়ি চালানো শিখল না। আমরা বাকিরা বন্ধুবান্ধবের গাড়ি নিয়ে লাইসেন্স করে নিজেরা গাড়ি কিনে ফেললাম, কিন্তু নৈব চ অভিজিৎ। জয়ন্ত বোধহয় ১৯৯০ সালে বিয়ে করে চাকরি নিয়ে ক্লীভল্যান্ড চলে গেল। অভিজিতের দরকার পড়লে পিকলু বা মণীশ বা অন্য কেউ ওকে গাড়িতে রাইড দেয়। ব্রিজ খেলে Lewiston-এ ট্রেন থেকে নামলে আমি নিয়ে আসি। এমনকি যখন Washington D C-তে গেল চাকরি নিয়ে, তখন অয়ন আর দেবাশিস ওকে পৌঁছে দিয়ে এল।
দ্বিতীয় এক অভিজিৎ এক বছরের জন্য Penn State-এ এসেছিল – সস্ত্রীক। মেয়েটির নাম পাপিয়া। আমেরিকায় Graduate student-দের গৃ্হবধূ বউরা অনেকেই baby sitting করত। লাইসেন্স ছাড়া, তাই তাদের চার্জও কম হত। উভয় পক্ষেরই সুবিধে। পাপিয়াও এরকম এক জাপানী পরিবারে কিছুদিন একটি ছোট বাচ্চার দেখাশোনা করেছিল। বাচ্চাটি পাপিয়া বলতে পারত না, বলত পোপো। আমরাও তাকে পোপো নামেই ডাকা শুরু করেছিলাম। অভিজিৎ আর পাপিয়া আমাদের চেয়ে বেশ একটু বড় ছিল বয়সে। বেশ কয়েক বছর চাকরি করে, এক বছরের ছুটি নিয়ে এসেছিল অভিজিৎ, Economics বা Business-এ। পোপো ওর সংসারের গপ্পো করত – যে ও কলকাতার বাড়িতে কিছুই করে না, এমনকি নিজের জামাকাপড়ও কাচে না; ওর শাশুড়ি নাকি ওর নোংরা শায়া, ব্লাউজ আলমারি থেকে বার করে কেচে দেন।
এহেন পোপো একদিন আমাদের অনেককে খেতে বলল। বাগীশা আর আমি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত – কিছু জুটবে তো, না কি রাতের বেলা পেটে কিল মেরে থাকতে হবে। ফোনে পরামর্শ করে আমরা ঠিক করলাম একটা কিছু রেঁধে নিয়ে যাব, ডাল বা কোনো একটা তরকারি। পোপো ভাত করবে, আর মাংস, আর আইসক্রিম ইত্যাদি তো থাকবেই। বন্ধু-বান্ধবদের নেমন্তন্ন করলে অনেক সময়েই আমরা এরকম ভাগাভাগি রান্না করে নিতাম। নিজেদেরই তো ব্যাপার।
আমেরিকাতে আমাদের সব অ্যাপার্টমেন্টে fire alarm থাকত। ঘরের ভেতরে ধোঁয়া হলেই সে বিদঘুটে রকম আওয়াজ করে বাজতেই থাকত, তাকে তখন চুপ করানো দায়। আর বাঙালী রান্না, বিশেষ করে মাছ ভাজা করলে ধোঁয়া হতে বাধ্য। অনেক বাড়িতেই fire alarm-এর ব্যাটারি খুলে রাখা হত। পোপোও তাই করেছিল। আর সেদিন আমাদের জন্য বেগুন ভাজতে বসেছিল।
বেগুন ভাজা কঠিন কাজ, অনেক তেল দিতে হয়, বেগুন সব তেল টেনে নেয়, ভাজা হয়ে গেলে আবার তেল ছেড়েও দেয়। বেগুন ভাজার রং হবে বাদামী, কিন্তু পুড়ে যাবে না। পোপো তো মনের আনন্দে বেগুন ভাজছে, তেল পুড়ছে, বাড়ি ভর্তি ধোঁয়া, দরজার তলা দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে, করিডোরে ধোঁয়াক্কার। সেখানকার অ্যালার্ম বাজছে, পোপো শুনতে পায়নি, কিন্তু প্রতিবেশিরা তো শুনেছে। তারা খবর দিয়েছে ফায়ার ব্রিগেডকে। ফায়ার মার্শাল এসে পোপোর দরজায় ধাক্কাধাক্কি করতে লেগেছেন। ততক্ষণে বেগুন ভাজা হয়েও গেছে। ফায়ার মার্শাল যখন বলছেন
- Hi, how are you doing?
পোপোর তখনও হুঁশ নেই। সে ও এক গাল হেসে ফায়ার মার্শালকে বলেছে
- I am doing fine. How are you doing?
Fire alarm-এর ব্যাটারি খোলা শাস্তিযোগ্য অপরাধ কি না জানি না, কিন্তু অবশ্যই বিপজ্জনক কাজ। ওদেশের বাড়ি তো বোর্ডের তৈরী, সব বন্ধ, আগুন লেগে যাবার সম্ভাবনা যথেষ্ট বেশি। সেদিনের মত পোপো একটু-আধটু ধমক খেয়েছিল, একটা কোনো কাগজেও সই করতে হয়েছিল, ‘এমন কর্ম আর করিব না’ বলে। তবে ফায়ার মার্শালকে পোপো বেগুন ভাজা খেয়ে যেতে বলেছিল কি না, এটা আর মনে নেই।
নাম বদলে যাওয়ার আরো দু-একটা গল্প বলি। জয়ন্ত ডিগ্রি পেয়ে State College থেকে চলে যাবার পরে অভিজিতের রুমমেট হযে যে ছেলেটি এল তাকে দেখেই বাগীশা বলে উঠল, “তোমাকে দেখে মনে হয় তোমার নাম রতন”। ব্যস, বাঙালী মহলে তার রতন নামটাই চালু হয়ে গেল। যদিও তার আসল নাম ছিল ভাস্কর।
দ্বিতীয় গল্পটা আরো পুরনো। প্রেসিডেন্সিতে ফিজিক্সের সহপাঠী ছিল শুভ্র দত্ত। কিন্তু তাকে আমরা জগা নামেই ডাকতাম, কারণ সে জগবন্ধু ইনস্টিটিউশন থেকে এসেছিল। আমরা যখন Penn State-এ, তখন সে Pittsburg-এর ছাত্র। সেখানে বেড়াতে গিয়ে আমি তার খোঁজ করছি জগা নামেই, আসল নাম তো ভুলে গেছি। সৌভাগ্যের বিষয় হল, প্রেসিডেন্সির ফিজিক্স বলাতে তাকে খুঁজে পেতে অসুবিধে হয়নি।
আরো কত গল্প আর অভিজ্ঞতা জমা আছে Penn State আর State College-এর বন্ধুদের নিয়ে। বন্ধুত্ব ব্যাপারটা খুব আশ্চর্যজনক বলে আমার মনে হয়। সেই যে বাউলরা গান গায় - যার সঙ্গে যার মজে মন! শুধু প্রেম নয়, বন্ধুত্বের ব্যাপারটাও একই রকম। তার নানান স্তর – স্কুল-কলেজে একরকম, চাকরিস্থলে আবার আর এক রকম। মণীশের স্ত্রী আমাকে একবার বলেছিল, “তুমি বাগীশাকে যেমন তুই বল, আমাকেও তাই বলো না কেন”? বাগীশা আমার ক্লাস ফাইভের বন্ধু, তায় আমি তার মামীশাশুড়ি - তাকে তুই বলব না তো কাকে বলব? একটু বয়সে আলাপ হলে চট করে সমবয়সীদের তুই বলতে পারি না। বয়সে অনেকটা ছোট হলে, তবে সেটা সম্ভব হতে পারে।
হোলি চাইল্ড আর বেথুনে শুধু মেয়েরাই পড়ত, প্রেসিডেন্সিতে প্রথম বান্ধব সহপাঠী জুটল। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলল ইউনিভার্সিটিতে, Penn State-ও। সেখানে সবাই ছাত্র, বা ছাত্রের সহধর্মিনী। জীবন সবাইকার প্রায় একই রকম – সকাল আটটায় ডিপার্টমেন্ট, বিকেল ছটায় ফেরা, আবার রাতে গিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চালানো, পরদিন PhD advisor-এর বকুনি খাওয়া, ক্লাস নেওয়া, খাতা দেখা, সপ্তাহান্তে বাজার, বাড়ি পরিস্কার ইত্যাদি। মাঝে মাঝে বেড়াতে যাওয়া। সেইজন্য আড্ডা হত সবাই মিলে একই সঙ্গে।
অস্টিনে চাকরি নিয়ে গিয়ে দেখলাম সেখানে বাঙালীরা একত্র হলে পুরুষ এবং মহিলাদের দুটো আলাদা গ্রুপ হয়ে যায়। আমার বয়সী মহিলারা প্রায় সবাই বিবাহিত এবং ছোট বাচ্চার মা। কোন বাচ্চার potty training কেমন ভাবে হয়, কাকে সোফায় বসাতে হয, কাকে কোলে নিতে হয় – স্বাভাবিকভাবে এসবে আমার আগ্রহ ছিল শূন্যের থেকেও কম। তাদের বেশির ভাগের সঙ্গেই আমার তাই বনল না। তাদের বরেদের আড্ডায় যোগ দিতে গিয়ে দেখি সেখানে খালি স্টকের ওঠানামা, বাড়ির দাম আর গাড়ির দামের আলোচনা চলছে। সন্তর্পনে সেখান থেকেও কেটে পড়তে হল।
অস্টিনে বন্ধুত্ব হল সমবয়সী জয়দীপ আর শান্ত, আর বয়সে অনেক বড় ইন্দিরাদি আর অশোকদার সঙ্গে। ইন্দিরাদি প্রায়ই নেমন্তন্ন করে খাওয়াতেন, শুধু আমাদের নয়, আরো অনেককেই। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই যখন বিদায় নিত, আমি ইন্দিরাদির ডেনে কার্পেটের ওপর লম্বা হতাম – অর্থাৎ এইবারে সিরিয়াস আড্ডার সময়।
যাদের গল্প বললাম তাদের অনেকে সঙ্গেই এখন আর যোগাযোগ নেই। আবার হঠাৎ হঠাৎ এক এক জনের সঙ্গে দেখা হয়েও যায়। যেমন আশিস-মীনাক্ষীর সঙ্গে বহুদিন পরে এয়ারপোর্টে দেখা – ওদের মেয়ের ভাবী শ্বশুরবাড়িতে দেখা করতে যাচ্ছে – যে মেয়েকে আমরা জন্মাতে দেখলাম State College-এ। সুরেশের সঙ্গে দেখা হল তিরিশ বছর পর। রবিপ্রদক্ষিণ পথে পৃথিবীর কক্ষ নির্দিষ্ট হতে পারে, কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র অণু-পরমাণুরা কখন কার কাছাকাছি চলে আসি তা সম্ভাবনাতত্বের এক্তিয়ারের বাইরে।




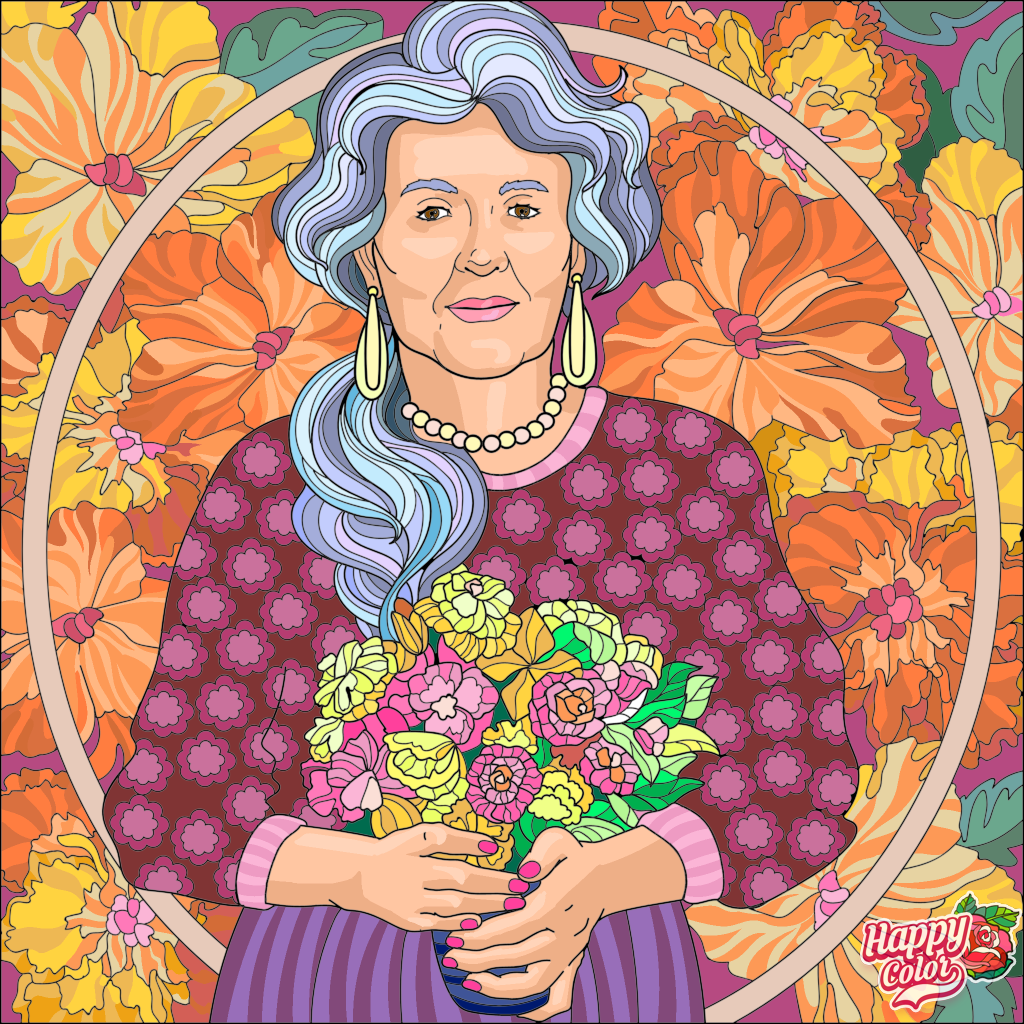
Penn State
No Giant Panda can fly, sudhu ei tagline e akta golpo hoye jay. Darun
Soma
26-07-2025 20:38:07