আফ্রিকান সাফারি আর বর্ন ফ্রি আমার অন্যতম প্রিয় বই হলে কি হবে, জন্তু জানোয়ার নিয়ে আদিখ্যেতা আমার বিলকুল না পসন্দ। কিন্তু আমার পছন্দ মতো জীবন থোড়ি চলে। কাকুর হাত ধরে, সেজেগুজে ৮ বি বাসের দোতলায় চড়ে রবিবার বড় পিসিমার বাড়ি যাওয়া খুব ই আনন্দের ব্যাপার ছিল ছোটবেলায়। সেখানে আদর আপ্যায়ন যত, গল্পের বই এর সমাহার ও তত । কিন্তু ১০০% আনন্দ কি জীবনে পাওয়া যায়! দাদাভাই এর ভয়ঙ্কর কুকুর প্রীতি। প্রথমে ছিল সিংহের মতো দুই অ্যালসেশিয়ান, তারপর কিছুটা শান্ত জিকো। গায়ের কাছে এসে গরম নিঃশ্বাস ফেলাটা ছিল দুচোখের বিষ, তার ওপর জিভ দিয়ে চাটা, মোটে বরদাস্ত হত না। এমন কি মানিকতলা বাড়ির তিন তলার ফ্ল্যাট এর ছোট পম কুকুরকেও একই কারণে পছন্দ ছিল না। সেটা আবার ভীষণ চিৎকার করতো আর মলি ভয় পেয়ে ছুটে পালাতো বলে ওকে তাড়া করতো।
উচ্চ মাধ্যমিকের আগে বেথুন কলেজের দারোয়ান ব্যাঙ ধরে দিতো ডিসেকশন এর জন্য। একবার একটা জ্যান্ত ব্যাঙ ধরে দিয়েছিলো। বাড়িতে এনে প্লাষ্টিক খুলতেই সেটা লাফিয়ে বেড়িয়ে কোথায় যে পালালো! মা এর চ্যাঁচামিচিতে বুঝলাম পুজোর জায়গায় উপস্থিত হয়েছে। মরা ব্যাঙ কাটতে পারলেও জ্যান্ত ব্যাঙ ধরা আমার সাধ্যাতীত। তবে চাকরি জীবনে আমার কোয়ার্টারে ব্যাঙ এর উপস্থিতি বেশ গা সওয়া হয়ে গিয়েছিলো।
পাশ করার পর প্রথম পোস্টিং মুর্শিদাবাদ এর নবগ্রাম । কোয়ার্টার এর উল্টোদিকে থাকতো প্রশান্ত, একটা বাচ্চা ছেলে, আমার ফাই ফরমাশ খাটতো। একটা ঘরে ওরা বাবা, মা, ভাই, বোন, বেশ কয়েকটা হাঁস, মুরগি, ছাগল একসঙ্গে থাকত। একবার কোনো কারণে ওদের বাড়ি গিয়েছি, সব হাঁস, মুরগি, ছাগল ঘর থেকে বেড়িয়ে আমায় বসার জায়গা করে দিলো। সে আতিথেয়তায় আমি মুগ্ধ। যদিও তাদের গায়ের গন্ধ সবটুকু সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে নি। যেটুকু রেখে গিয়েছিলো তাতে বেশিক্ষণ বসা সম্ভব ছিল না। এর পরের পোস্টিং সাগরদিঘি। সেখানে পাশের কোয়ার্টার এ সহপাঠী বালা সস্ত্রীক। ওরা হঠাৎ একটা টিয়াপাখি নিয়ে এলো। তারপর তাকে খাওয়ানোর কি ধুম! জানিস, ও আজ লঙ্কা খেয়েছে, আম খেয়েছে, ভাত খেয়েছে! একদিন বালা র বৌ মৌসুমী র হাতে ঠুকরে রক্ত বের করে দিলো, তবু ভালোবাসা কমে না। শেষে একদিন উড়ে পালাল। ওরা খুব মনমরা হয়ে রইলো।
পড়ানোর চাকরি করতে ঢুকলাম ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে। ওখানে কোনো টিচার যদি বলতেন আজকাল ছেলেদের সামলানো যায় না, তাকে এই বলে সিনিয়ররা সান্ত্বনা দিতেন যে, এ আর কি, তোমার ক্লাসে তো ভেড়া ঢুকিয়ে দেয় নি। খুব কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইলাম ক্লাসে ভেড়া ঢোকানো কি ব্যাপার! সে গপ্পো শুনে চক্ষু চড়কগাছ। কালচার বানানোর জন্য মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্ট কে ভেড়া পুষতে হত। তাদের ঘাস খাওয়ার একটা জায়গা ছিল, যেটা লেকচার থিয়েটারের খুব কাছে। একজন "ছাত্র অবান্ধব" শিক্ষকের ক্লাসে ছেলেরা ওই ভেড়া ঢুকিয়ে দিয়ে ক্লাস ভণ্ডুল করে দিয়েছিলো। সেই থেকে ছেলেরা ঝামেলা করলে আমি ও ভাবি, আমার ক্লাসে তো কেউ ভেড়া ঢুকিয়ে দেয় নি!
সব মেডিকেল কলেজে এনিম্যাল হাউস রাখা একসময় বাধ্যতামূলক ছিল। আমার যখন সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজে পোস্টিং, যেটি তখন সবে তৈরী হচ্ছে। একটি মাত্র এ. সি. ঘর থেকে আমরা বিতাড়িত হলাম, কারণ ওই ঘরটিকে এনিম্যাল হাউস করা হবে। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে কেনা হল খাঁচা, সাদা ইঁদুর, খরগোশ, তাদের খাবার জন্য টাকাও বরাদ্দ হল। সকাল থেকে গাজর কুচি করা হচ্ছে, খরগোশ খাবে। আমাদের কোন ছাত্র ভরতি হয় নি তখনও, তাই এই সব দেখে সময় কাটছে। কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য খরগোশ এত দ্রুত বংশ বিস্তার শুরু করল যে এনিম্যাল হাউস পরিষ্কার রাখাই সমস্যা। ক্রমশ আমরা ওখানে যাবার উৎসাহ হারিয়ে ফেললাম।
তবে ঠিকঠাক এনিম্যাল হাউস দেখেছিলাম এম.ডি. পড়ার সময়। সেবাগ্রাম মেডিকেল কলেজের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ রিসার্চ ল্যাবরেটরি হিসেবে বিখ্যাত। ফাইলেরিয়া নিয়ে কিছু অভিনব আবিষ্কার সেখানে হয়েছে। ওখানে ফাইলেরিয়ার মশা পালন হয়। মশারা থাকে মশারিতে আর আমরা বাইরে থেকে তাদের দর্শন করি। খরগোশ আছে। তাদের লম্বা কানের ওপর যে শিরা থাকে সেখান থেকে রক্ত নিতে হয়। একটা গাজর দিয়ে একটু আদর করে বনি আর স্বাতী ওদের কান থেকে রক্ত নিতো। ওরা চুপ করে থাকতো, নড়তো না একটুও। এনিম্যাল হাউস এ রিসার্চ স্কলারদের ডিউটি ভাগ করা থাকতো, কিভাবে এনিম্যাল হাউস মেন্টেন করা হয় সেটা ওদের রীতিমতো হাতেকলমে শিখতে হতো। এনিম্যাল হাউসের লাগোয়া বারান্দায় বাঁধা থাকতো একটি ছাগল, সেও এনিম্যাল হাউসের বাসিন্দা, কিন্তু ঠান্ডা ঘর তার জন্য নয়, তাকে টি. বি র এন্টিজেন ইনজেকশন দেওয়া হতো, তারপর তার রক্ত নিয়ে দেখা হতো কত দিনে কত এন্টিবডি তৈরী হচ্ছে। এই ছাগলটির দেখাশোনার জন্য আলাদা লোক রাখা ছিলো। সে নিয়মিত ছাগল চড়াতে নিয়ে যেত, ইনজেকশন দিয়ে জ্বর এলে তা মাপতো, ওষুধ দিতো আর রক্ত পরীক্ষার দিন রক্ত নিতো। সেই লোকটি হঠাৎ ছুটি নিয়ে দেশের বাড়ি চলে গেলো। বাকি সব কাজ ডিপার্টমেন্টের সবাই ভাগাভাগি করে করলেও রক্ত টানার কেউ নেই। সবাই আমাকে ধরলো। আমি পত্রপাঠ না বলে দিলাম। তারপর যে পরিমাণ সাধ্য সাধনা সবাই মিলে করলো, সারা জীবনেও কেউ অত সাধে নি। নানা অসম্ভব, অবাস্তব শর্ত আরোপ করেছিলাম। সবাই তাতেই রাজী। অগত্যা কি আর করা। বেজার মুখে একটা বই পড়ে আর ছবি দেখে বিশাল সিরিঞ্জ এবং বিশালতর বাহিনী নিয়ে অকুস্থলে হাজির হলাম। সবুজ ঘাসের ওপর ছাগল কে শোয়ানো হলো। দুজন দুই দুই চার হাতে ছাগলের চারটি পা ধরলো। একজন ছাগলের মাথা কোলে নিয়ে বসলো। আর একজন ছাগলের গায়ে মাথায় হাত বোলাতে লাগলো। অন্য একজন স্পিরিট দিয়ে শিরার ওপরের চামড়া মুছে দিয়ে বললো, এই দেখ, শিরা দেখা যাচ্ছে, টানো। আমি শিরার ওপর হাত দিয়ে দেখি, ওরে বাবা, কি খসখসে আর মোটা চামড়া। ছুঁচ ঢুকলে হয়! জয় মা, বলে দিলাম ঢুকিয়ে ছুঁচ, এবার পিস্টন টানতেই, আসছে, আসছে শব্দ। সবার মনোযোগ ছাগলের দিকে, আদিখ্যেতাও বাড়ছে! এই তো... আর একটু... হয়ে গেলো...
আমাকে পাত্তাই দিচ্ছে না আর! কাজ হয়ে গেলো কি না! সব শুনে বাবা বললো, গবেষণা মানে তো গো + এষণা, তা তোর গরু খোঁজার সাথে সাথে ছাগলেষণাও হয়ে গেলো!
শুধু ছাগলেষণা? সারা জীবন ধরে কত যে “এষণা” সে কথা বলতে গেলে তো মহাভারত হয়ে যাবে।


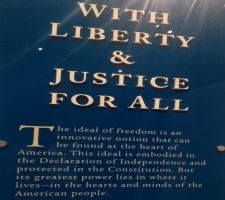


Pashupalan
Enjoyed reading this.
Mamata Dasgupta
18-06-2021 21:27:07